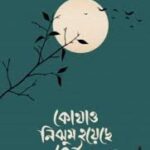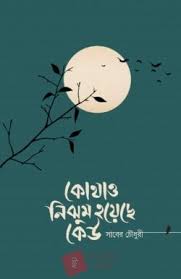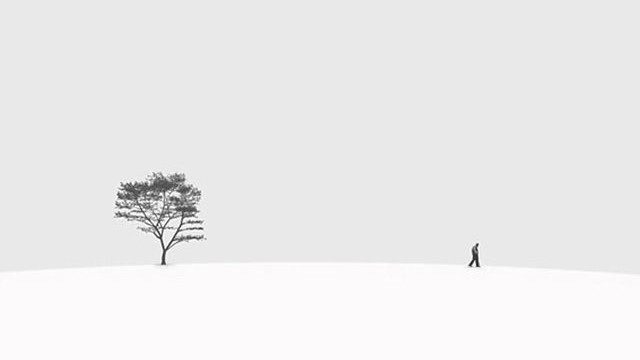আবুল মনসুর আহমদ বাংলাদেশের কালচার বইয়ে ‘আমাদের ভাষা’ শিরোনামে সাংস্কৃতিক বিবেচনা থেকে বাংলা ভাষার নতুন এক ভাষা-প্রকল্পের কথা বলেছেন। এ আলোচনাটি তিনি বিক্ষিপ্তভাবে নানা জায়গায় করলেও, এ প্রবন্ধটিতে মোটামুটি বিস্তৃতভাবে একে ব্যাখ্যা করেছেন। এ আলোচনাটি তিনি করেছিলেন ১৯৫৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে। এরপর বহু সময় গড়িয়েছে, কিন্তু তা আজো সমান প্রাসঙ্গিক এবং সমকালে এটি সাহিত্যিক ও ভাষাগবেষকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে আবার আলোচিত হতে শুরু করেছে। বিশেষত তরুণদের মধ্যে একটা প্রস্তুতির আলামত দিন দিন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানে আমরা সংক্ষিপ্ত বয়ানে তার প্রকল্পটি বুঝার চেষ্টা করব, এবং সাথে মাঝে মাঝে কিছু মন্তব্যও যুক্ত করব।
আবুল মনসুর আহমদ বলেন :
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্রষ্টা মূলত বাংলার নবাব-বাদশারাই। তা-ই বাংলার মুসলমানদের নিজস্ব ভাষা। কিন্তু প্রায় দুইশো বছরের ইংরেজ শাসনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে, এবং উন্নতিও সাধিত হয়েছে বটে, তবে একই সাথে তা ভাষাটিকে মুসলমানদের থেকে দূরেও নিয়ে গেছে।
উনিশ শতকের গোড়া হতে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বাংলা ভাষা ছিল পণ্ডিতি ভাষা। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে টেকচাঁদ ঠাকুর, দ্বিজেনঠাকুর ও রবিঠাকুরে শক্তিশালী কলমের জোরে সেটা জনগণের ভাষায় এলেও তা কেবল সিলেক্টিভ জনগণ—পশ্চিম-বাংলার মধ্যবিত্তশ্রেণীল ভাষা হতে পেরেছিল। সার্বজনীন বাংলার জনগণের ভাষা হতে পারেনি। কেননা, এই আসল জনগণের ভিতর মুসলমানরাও রয়েছেন, এবং বাংলা ভাগ হওয়ার আগে-পরে সবসময়ই মুসলমানদের ভাষা নানা বৈশিষ্টে স্বতন্ত্র ও স্বকীয় ছিল ও আছে। কিন্তু মুসলমানদের ভাষা উপেক্ষিতই থেকে গেছে তাদের কাছে। নজরুল এসে সে জায়গাটাতে সফলভাবে দ্রোহ ছড়িয়ে গেলেও সার্বিক কোন সমাধান শেষ পর্যন্ত আসেনি।
তাঁর মতে দুই বাংলার ভাষার ব্যবধান নানা ভাবে পরিলক্ষিত হয়, উদাহরণত–
১. কৃষ্টিক ইমেজগত শব্দ-ব্যবধান। অর্থাৎ, প্রচুর শব্দ আছে যেগুলো বাঙালি মুসলমান ব্যবহার করেন, কিন্তু হিন্দুগণ করেন না। সে জায়গায় তাদের আলাদা শব্দ রয়েছে। যেমন, জল ও পানি। একটা শব্দ কোন পরিমণ্ডলে ব্যবহৃত হতে হতে তার একটা কালচারাল ইমেজ তৈরী হয়। ফলে, মুসলিম সমাজে ব্যবহৃত কোন শব্দে ইসলাম উপস্থিত না থাকলেও, মুসলমানিত্ব অবশ্যই থাকে। ফলে, সে শব্দকে এড়িয়ে চলার মধ্যে ইসলামকে এড়িয়ে চলা না হলেও মুসলিম মানসকে ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করার ত্রুটি রয়েছে। এবং মুসলমানদের জন্য তা ঐতিহ্যচ্যুতির ব্যাপার।
অবশ্য, তিনি পশ্চিম-বাংলার শব্দগুলোকে বিলকুল পরিত্যাগ করার কথাও বলেন না। এখানে এসে একটু ধাঁধাঁ তৈরী হয়। কিন্তু আমরা যদি তার মূল বক্তব্যটি ধরতে পারি, তাহলে এই ধাঁধাঁটি থাকবে না। তিনি বলতে চেয়েছেন, মুসলিম সমাজের ভাষায় মুসলিম মানস প্রতিফলিত হোক। একটা সমাজের ভাষা গড়ে উঠুক সেই সমাজের গভীর থেকে। কথা তার এতটুকুই। কিন্তু, তা হয়নি। এখানে পানিকে পরিকল্পিতভাবে এবং উন্নাসিকতা দেখিয়ে এড়িয়ে গিয়ে জলকে গ্রহণ করা হয়েছে। এটা অসঙ্গত ও অন্যায়। ফলে, সারকথা এই যে তিনি সঙ্গতিকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চান এবং পরিকল্পিত অন্যায়কে রোধ করতে চান।
২. ক্রিয়াপদের পার্থক্য।
৩. বিশেষ্য প্রভৃতির পার্থক্য।
৪. নিছক অনেক দেশি শব্দেরও পার্থক্য আছে, যার বেশিরভাগ ধরা পড়ে উচ্চারণে। যেমন, তুলা আর তুলো।
মুসলমান বাঙালির ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, এতে প্রচুর পরিমাণ উর্দু আরবি ফার্সির মিশ্রণ থাকার ফলে এটি গোটা ভারত উপমহাদেশের বোধগম্যতার বেশি কাছাকাছি, এর বিপরীতে পশ্চিম-বাঙলার বাঙলাটি এই দিক থেকে খুবই সীমিত হয়ে পরিসরে আবদ্ধ। অবিভক্ত বাংলায় হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল, তাই বাংলা ভাষা ছিল হিন্দু কালচারের বাহক, মুসলমান কালচারের বাহন তো ছিল না-ই, বরং এর প্রতি ছিল দারুণ বিরূপ। তিনি এই উপেক্ষা ও বিরূপতার বিপক্ষে ছিলেন।
এখানে একটা জিনিস খুব সতর্কতার সাথে বুঝে রাখতে হবে, হিন্দু-মুসলমানের ভাষার এই ব্যাবধানকে তিনি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করছেন না। করছেন স্বভাব-প্রবণতা, মানসিক স্বস্তি ও কালচারাল যুক্তির ভেতর থেকে। এ বিষয়টি আরো বিশদভাবে তিনি পরিস্কার করেছেন এ বইয়ের ‘সাহিত্যের প্রাণ রূপ ও আংগিক’ শিরোনামের আরেকটি প্রবন্ধে। সেখানে তিনি বলেন :
“সাহিত্যকে কাল ও স্থানের প্রভাবে আসিতে হয় আরেক কারণে। সাহিত্য আসলে ফিলিং (অনুভূতি), ইমোশন (ভাবাবেগ) ও ইমাজিনেশনের রূপায়ণ। এই ফিলিং ইমোশন ও ইমাজিনেশনের গোড়াতে নিশ্চয়ই ব্যক্তি। ব্যক্তি স্থান ও কালের একটি ইউনিট।… যত বড় বিশ্ববাণীই প্রচারিত হউক না কেন, সেটা হইবে ব্যক্তির মুখ দিয়া এবং সে ব্যক্তি কথা বলিবে একটি জায়গায় দাঁড়াইয়া একটি সময়ে। এই ব্যক্তিটি লেখক, জায়গাটি তার দেশ, সময়টি তার বর্তমান। ব্যক্তি, স্থান ও কালের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রূপায়িত হয় ভাষায়…”
এবং একটু সামনে গিয়ে তিনি উদাহরণ হিসেবে আনেন ইংলেন্ড ও আমেরিকার নিজস্ব ইংরেজি পদ্ধতির কথা। সেখানে ধর্ম, ধর্মভিত্তিক কৃষ্টি ও চার্চ এক হওয়া সত্তেও কালচারাল স্বকীয়তার প্রশ্নে মার্কিনীদেরকে আলাদা ভাষা গড়ে তুলতে হয়েছে; আর, আমাদের মধ্যকার ধর্মীয় ব্যবধান, ধর্মভিত্তিক সাংস্কৃতিক ও জীবনাচারের ব্যবধান সত্তেও সমাজের নিজস্ব ভাষা এড়িয়ে পশ্চিমের অনুকরণ করে যাওয়া একটা হীনমন্যতা ও অনাবশ্যক কৃত্তিমতা। তার আপত্তি ছিল এ জায়গাতেই। এতে একটা বাস্তবতাকে এড়িয়ে চলা হচ্ছে, এবং তার প্রতি বিরূপতা প্রদর্শন করা হচ্ছে।
আবুল মনসুর ভাষা সংক্রান্ত এই আলাপে শুধু সাহিত্যের ভাষা নিয়ে আলোচনা করেননি। সাহি্ত্য তো ভাষার সীমিত ব্যবহার। স্কুল-কলেজ-মাদরাসায় পাঠদানে, অফিস-আদালতে, রেডিও-টেলিভিশনে, নানা অঞ্চলের নানা উচ্চারণের মানুষের পারস্পরিক বুঝাবুঝিতে—অর্থাৎ, রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সকল স্তরে যে মান ভাষাটি ব্যবহার করি, তার আলাপ হলো সে ভাষা নিয়ে। সে জায়গাটিতেই আমরা প্রমিতের কৃত্রিমতায় আটকে আছি। এখান থেকে আমাদেরকে নিজস্ব স্বস্তির দিকে ফিরে আসতে হবে।
এখন, এই ব্যবধান কি শুধু কিছু শব্দ আর গল্প উপন্যাসের চরিত্র পাল্টে ফেললেই হবে? তাঁর মতে মূল থেকে বাস্তবতার আলোকে একটি নতুন ভাষাকে গড়ে তোলাই হলো এর প্রকৃত সমাধান। এর জন্য তিনি প্রস্তাব করেছেন, আমাদেরকে দুইটি কাজ করতে হবে—পূর্ব বাংলাকে গঠন করার জন্য এদেশের মুসলিম সমাজের নয়া কালচারের বাহক নয়া সাহিত্য সৃষ্টি করা। দু্ই. পূর্ব পাকিস্তানের সকল অঞ্চলের বোধগম্য একটি ঢাকাইয়া কথ্য বাংলা গড়ে তোলা। কারণ, ভাষা ও সাহিত্য রাজধানীকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। আগে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের রাজধানী ছিল কলকাতা, দেশ ভাগের পর রাজধানী হয়েছে ঢাকা। সুতরাং, ঢাকাসহ অন্যান্য শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাংগালী ভদ্রলোকের কথ্য ভাষাই হবে আমাদের সাহিত্যের ভাষা। তারা তাদের অফিসে আদালতে ক্লাবে বৈঠকখানায় স্কুলে কলেজে যে ভাষায় কথা বলেন, যে সব শব্দ ও ক্রিয়াপদ যে স্বর-ভংগিতে যে বাক-প্রণালীতে ব্যবহার কনে, সে সফিস্টিকিটেড উচ্চারণ-ভংগীর কথ্য ভাষাই হবে আমাদের সম্মিলিত মান ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যম। সকলের বোধগম্যতার জন্যই এটা দরকার। এর জন্য একটা নিউক্লিয়াসের দরকার পড়বে। কলকাতার নিউক্লিয়াস ছিল শান্তিপুরী ভাষা, আমাদের নিউক্লিয়াস হতে পারে বিক্রমপুরের ভাষ্য-ভংগীটি। এবং আমাদের পাড়াগাঁয়ে হাজার হাজার চলতি শব্দ অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে, সেগুলোকে মান ভাষায় গ্রহণ করতে হবে।
নতুন এই ভাষার ক্ষেত্রে ঢাকাকে কেন্দ্র করে সকল জেলা ও অঞ্চলের সমন্বয়টি কীভাবে হতে পারে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন বিস্তারিত নির্দেশনা আবুল মনসুর দিতে যাননি, হয়তো ইচ্ছে করেই। তিনি শুধু চেয়েছেন প্রতিষ্ঠিত প্রমিতায়নের কৃত্রিমতা থেকে আমরা যেন নিজস্ব স্বস্তির দিকে একটি সম্মিলিত যাত্রা শুরু করি এবং এ ব্যাপারে একটা কর্মযজ্ঞকে গড়ে তুলি।
তাই তিনি বলছেন, প্রতিষ্ঠিত প্রমিতায়নের কৃত্রিমতা থেকে বেরিয়ে আমরা জীবন থেকে তুলে আনা যে স্বাভাবিক বাংলার কথা বলছি, সে স্বাভাবিক বাংলা কী, কিভাবে গঠিত হয়, তার রূপ কী হবে—এগুলো নির্ভুলভাবে বিচার, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা দরকার। এবং সে সময়ে বিশেষ কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে :
১. ভাষা ও সাহিত্যের রাজধানী হবে ঢাকা।
২. পদ্মার পশ্চিম পাড় এখন কলকাতার বদলে ঢাকার দিকে নজর দিতে শুরু করেছে।
৩. পশ্চিম-বাংলার ৪০ লাখের মত মুসলমান এ বাংলায় স্থায়ী হয়েছেন, কথ্য ভাষায় ও সাহিত্যে তাদের ছাপ থাকবে।
৪. পূর্ব-পাকিস্তানের জেলাগুলোর মধ্যে যে ভাষাগত ব্যবধান তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উচ্চারণগত ব্যবধান।
৫. দশ লাখের মত উর্দুভাষী মুসলমান এ দেশে স্থায়ী হয়েছেন, নতুন ভাষাটিতে তাদের প্রভাবও থাকবে।
৬. বাংলা ভাগের আগে কলিকাতার ঠাকুর পরিবারের মত বাংলা-ভাষী কোন প্রভাবশালী উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল না।
৭. ঢাকাতে দেশভাগের আগে আগে বাংলা-সাহিত্যে পূর্ব-বাংলাবাসী প্রভাবশালী কোন সাহিত্যিক গোষ্ঠি ছিল না। ফলে পুর্ব-বাংলার ভাষা ও সাহিত্যরীতির ছাপও এতে থাকবে। সে ছাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমাদেরকে একটা সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।
সুতরাং, সাহিত্যের বাহন হিসেবে কথ্য ভাষাকে গড়ে তুলতে গেলেও এসবের কারণে হরেক ভাষার সংমিশ্রণ হয়ে আমাদের নয়া ভাষাটি একটা খিচুড়ি ভাষা হবে। তবে, তা যেন জগাখিচুড়ি না হয়ে সুস্বাদু ভূনা খিচুড়ি হয়, সে জন্য কিছু টুটকা আমরা মেনে চলতে পারি।
১. নতুন জটিলতার আমদানি করা যাবে না। যেমন, ‘দেখিতেছি’কে ‘দেখতেছি’ না বলে ‘দেখছি’ বলা। কারণ, দেখছি দ্বারা এ বাংলার মানুষ সম্পন্ন হয়ে যাওয়া কর্মকেই বুঝায়। অপরদিকে ‘দেখতেছি’র সময়টি এপার-ওপার সকলের কাছেই বোধগম্য।
২. বিভিন্ন আঞ্চলিক উচ্চারণকে হুবহু ভাষায় ফুটানোর চেষ্টা না করা।
৩. পশ্চিম বাংলার অনুকরণে ‘ইয়া’ যুক্ত ক্রিয়াপদকে অতিরিক্ত মোচড়ানোর চেষ্টা না করা। যেমন, কেতাবি ভাষার ‘সরাইয়া’ এর স্থলে ‘সরায়ে’’ বলা; ‘সরিয়ে’ না বলা।
অন্য ভাষা থেকে আসা পরিভাষাগুলোর স্থলে জোর করে নতুন বাংলা পরিভাষা আবিস্কারের প্রয়োজন নেই। যা চালিত হয়ে মানুষ গ্রহণ করে ফেলেছে, তা বাংলা ভাষা হিসেবেই গৃহীত হবে, সেটা ইংরেজি হোক বা অন্য কোন শব্দ। কারণ, যে কোন চলতি শব্দই বাংলা শব্দ। বাংলা ভাষায় ইংরেজি শব্দ গ্রহণের ব্যাপারে তিনি প্রচুর পরিমাণ উদারতা দেখিয়েছেন। তিনি মনে করেন, ইংরেজি শব্দ যদি মানুষের জীবনযাপনের স্বস্তি ও স্বতঃস্ফুর্ততা থেকে উঠে আসে, তাহলে সেগুলোকে জোর করে বিতাড়িত করার কোন অর্থ নাই। এমনিভাবে, আত্মপরিচয়ের এই প্রকল্প বাস্তবায়ন এক দিনের কাজ নয়। কলকাতারও প্রথমে নিজস্ব ভাষা ছিল না। কিন্তু তারা গড়ে তুলেছে, আমাদেরকেও সেই অভিযাত্রা শুরু করতে হবে।
আবুল মনসুরের এই প্রকল্প ভাষা ও সাহিত্যচিন্তার কোন আনন্দ-কল্পনা থেকে উঠে আসেনি। এসেছে তিনি যে স্থান ও কালে দাঁড়িয়ে কথা বলেছেন, তার বাস্তব জীবনের অভিব্যক্তি থেকে। ফলে, এই প্রকল্প পুরোপুরি বাস্তবায়িত হওয়া অথবা নিঃশেষ ও বিস্মৃত হওয়ার আগ পর্যন্ত সকল কালেই তা প্রাসঙ্গিক হয়ে থেকে যাবে। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যে চিন্তা উঠে আসে সমাজ-জীবনের গভীর থেকে তা মূলত একটি পথকে নির্দেশ করে, পরবর্তী অভিযাত্রিগণ হয়তো প্রকল্পটিকে অক্ষুণ্ন না রেখে নিজের মত করে একে পূর্ণতা দিয়ে ক্রমশ এগিয়ে যান, কিন্তু সে প্রকল্প কালের গর্ভে বিস্মৃত হয় না, নিঃশেষিতও হয় না। একটি চিন্তার স্বার্থকতা মূলত এখানেই।